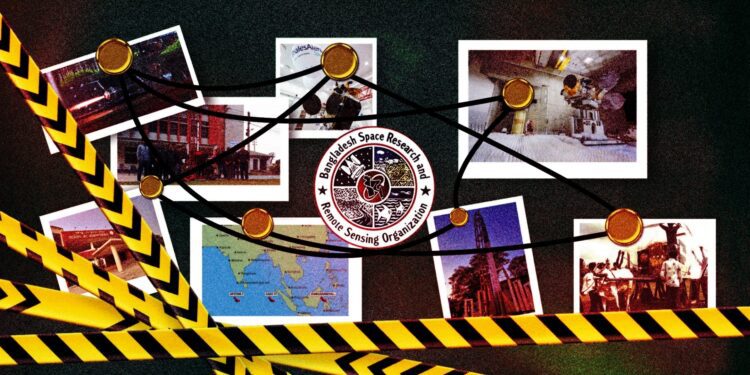গত বছর Starship Rocket Booster এর Chopstick Landing এর পর ফেসবুক ভেসে যায় ইলন মাস্কের প্রশংসায়। আপনি নিজেও হয়তো শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, স্ট্যাটাসে হয়তো লিখেছেন “মাস্ক লোকটা পাগল!” কখনো কি ভেবে দেখেছেন যে আটলান্টিকের ওপারের এক প্রাইভেট কোম্পানির মহাকাশ গবেষণায় সাফল্যের পর যে বাংলাদেশের মানুষ এতটা উচ্ছ্বসিত হয়, সে দেশের মহাকাশ গবেষণার অগ্রগতি কতদূর? আজ চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে SPARRSO কে নিয়ে।
প্রতিষ্ঠার ৪৫ বছরেও স্পারসোর কোনো অর্জন চোখে পড়ে নি দেশবাসীর। প্রকৃতপক্ষে স্পারসো কোনো মহাকাশ গবেষণা সংস্থাই না। মহাকাশ গবেষণা সংস্থা হতে হলে বাধ্যতামূলকভাবে নিজস্ব স্যাটেলাইট প্রযুক্তি প্রোগ্রাম থাকতে হয়; যা স্পারসোর নেই। আপনি হয়ত ভাবছেন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের কথা, অর্থনৈতিকভাবে লস হলেও অন্তত প্রযুক্তিগত দিক থেকে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করার কথা? গুড়ে বালি! স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে তাদের অবদান আছে বলে স্পারসো দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধু–১ উৎক্ষেপণে স্পারসোর কোনো সম্পৃক্ততাই নেই। স্যাটেলাইট ডিজাইন ও ম্যানুফ্যাকচার করেছে ফ্রান্সের থ্যালিস অ্যালেনিয়া স্পেস এবং লঞ্চ করেছে মাস্কের স্পেস–এক্স।
আচ্ছা নিজে ম্যানুফ্যাকচার করতে না পারার বা লঞ্চ না করতে পারার অনেক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু স্যাটেলাইট অপারেট তো করার কথা স্পারসোর। এমন কিছু ভাবলে আপনার এই আশাতেও বালি! স্যাটেলাইট অপারেট করে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট–১ পরিচালনার জন্য ২০১৭ সালে সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে BSCL প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার মূল লক্ষ্যই স্যাটেলাইট ও সংশ্লিষ্ট সেবায় স্বনির্ভরতা অর্জন করা।

অর্থাৎ, ৪৫ বছর ধরে অপারেশনাল থাকা দেশের একমাত্র মহাকাশ গবেষণা সংস্থার সাথে দেশের প্রথম স্যাটেলাইটের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো সম্পৃক্ততাই নেই! এমনকি স্যাটেলাইট সংশ্লিষ্ট গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং পরবর্তী স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনা করার দায়িত্বেও আছে BSCL! বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট–২ নিয়ে একটু পর আলোচনায় আসছি। আগে স্পারসোর সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিই।
Space Research and Remote Sensing Organization তথা স্পারসো বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সরকারি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। সর্বপ্রথম ১৯৬৮ সালে পরমাণু শক্তি কমিশনে আমেরিকার অটোমেটিক পিকচার ট্রান্সমিশন স্পেস প্রোগ্রামের গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপন করার মাধ্যমে বাংলাদেশে মহাকাশ প্রযুক্তির যুগ শুরু হয়। এই গ্রাউন্ড স্টেশনের মাধ্যমে স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি আবহাওয়ার খবর পাওয়া যেত। ১৯৭২ সালে নাসা প্রথম Earth Resources Technology Satellite (ERTS) উৎক্ষেপণ করলে শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বাংলাদেশে ERTS প্রোগ্রাম এবং Space and Atmospheric Research Centre (SARC) চালু করা হয়। পরবর্তীতে ERTS কে Bangladesh Landsat Satellite Program (BLP) হিসেবে পুনঃ নামকরণ করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে SARC ও BLP কে একীভূত করে ১৯৮০ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীন স্পারসো প্রতিষ্ঠিত হয়।
স্পারসোর মিশন হলো মহাকাশবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি, বন, সমুদ্রবিজ্ঞান, মহাকাশ ও বায়ুমণ্ডল, পানিসম্পদ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে গবেষণার দ্বারা অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস দেওয়া। মহাকাশ প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই এর মূল লক্ষ্য। স্পারসোর ব্যর্থতার পাল্লা ভারী, কারণ এর সাফল্যের পাল্লা একেবারেই ফাঁকা! এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে মোটা দাগে কিছু বিষয়কে দায়ী করা যায়।
-
প্রথম সমস্যা হচ্ছে টাকা।
২০২৪–২৫ অর্থবছরে ২৫টি গবেষণা খাতে স্পারসো মোট বরাদ্দ পেয়েছে ২ কোটি ১০ লাখ ৭৫ হাজার ১৭৫ টাকা। ২০১৯–২০ থেকে ২০২৪–২৫ পর্যন্ত গত ৫ বছরে মোট ৮৩টি গবেষণা প্রজেক্টে সর্বসাকুল্যে স্পারসো ৭ কোটি ৭৯ লাখ ৬০ হাজার ৬৯০ টাকা বরাদ্দ পেয়েছে। স্পারসোর একটি গবেষণা প্রকল্পের জন্য সর্বনিম্ন বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৫০০০ টাকা, যা ২০২১–২২ অর্থবছরে Trend of Rainfall Related Low Pressure System in Bangladesh এর জন্য অনুমোদিত হয়।

একই বছর Investigation on the Applicability of Microwave and Optical Satellite Images for Assessment of Rice Crop Area at Early Stage of Crop life Cycle (Phase 2) শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের জন্য ৬৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা গত ৫ বছরে সর্বোচ্চ।

প্রতিবেশী ভারতের সাথে তুলনায় না গেলেও পাকিস্তানের সাথে অবশ্যই তুলনায় যাওয়া উচিত। পাকিস্তানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা SUPARCO এর ২০২৪–২৫ অর্থবছরের জন্য ৬৫.৬১ বিলিয়ন রুপি প্রস্তাব করেছে পাকিস্তান সরকার। স্পারসো একটি গবেষণা ও প্রায়োগিক প্রতিষ্ঠান হলেও প্রতিষ্ঠার ৩০ বছর পর ২০১০ সালে প্রথম গবেষণার জন্য তহবিল দেওয়া শুরু করে সরকার। আলাদা বরাদ্দ দেওয়ার আগে স্পারসোর বিজ্ঞানীরা স্বতন্ত্রভাবে কিংবা কোনো প্রকল্পের আওতায় গবেষণা করতেন।
-
স্পারসোর ব্যর্থতার দ্বিতীয় কারণ এখানকার কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীরা।
প্রথম আলোর ২০২২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, স্পারসোতে মোট ১৬৯টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ৯১ জন কর্মরত আছেন। নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আছে স্পারসো বোর্ডের, সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত ১ জন চেয়ারম্যান ও ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে এই বোর্ড গঠিত হয়।
২০২৩ এর আগস্টে ভারতের চন্দ্রবিজয়ের পর প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা কৃষিবিদ আব্দুস সামাদ এর স্পারসোর চেয়ারম্যান হওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার তুমুল ঝড় উঠলে তাকে সংসদ সচিবালয়ে বদলি করা হয়। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের পঞ্চদশ ব্যাচে যোগদান করে পর্যটন কর্পোরেশনসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করে পদোন্নতি পেয়ে স্পারসোতে জয়েন করেছিলেন। এখান থেকেই প্রশ্ন ওঠে স্পারসোর নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং কর্মকর্তাদের যোগ্যতা নিয়ে। মজার ব্যাপার হচ্ছে যেই যোগ্যতা নিয়ে আপনি নাসাতে কাজ করতে পারবেন, একই যোগ্যতায় আপনি স্পারসোর কিছু কিছু পদে আবেদনই করতে পারবেন না!

স্পারসোর চেয়ারম্যান হিসেবে সাধারণত বিসিএস ক্যাডারদের নিয়োগ দেওয়া হয়। সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায় প্রশাসনে লেখাপড়া করেছেন এমন লোকেরাও অতীতে স্পারসোর চেয়ারম্যান পদে যোগ দিয়েছেন। তারা প্রশাসন ক্যাডার থেকে এসে মহাকাশ বিষয়ে শিখতে শুরু করেন। শিখতে শিখতে আবার তাদের অন্য দপ্তরে বা অবসরে যাওয়ার সময় হয়ে যায়। বর্তমান চেয়ারম্যানের দায়িত্বে আছেন মোঃ রাশিদুল ইসলাম, তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব।

২৯ ডিসেম্বর, ২০২১ এর একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী স্পারসোতে চতুর্থ গ্রেডের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার পদে আবেদন করতে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মহাকাশ বিজ্ঞান/ রিমোট সেন্সিং বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি সহ সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা অন্য কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় প্রথম শ্রেণীর চাকরিতে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৪৩ বছর হলেও অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভাইভা দিতে হয়।
এদিকে ভারতের ISRO–তে প্রকৌশলী বা বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্য দিতে হয় অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ICRB পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় আবেদনের যোগ্যতা হিসেবে প্রার্থীদের অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজিতে আবেদনকৃত পদের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি থাকতে হবে। এছাড়া বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনিয়ার ‘এসডি’ পদে আবেদনের জন্য অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি এবং ৬০% নম্বর থাকতে হবে। আবার নাসায় বিজ্ঞানী হিসেবে নিযুক্ত হতে হলে আবেদনকারীর কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং, পদার্থবিজ্ঞান, জৈবিক বিজ্ঞান, গণিত অথবা কম্পিউটার সাইন্সে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে। এছাড়াও এসকল ক্ষেত্রে অন্তত ২ বছরের পেশাদারি অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
স্পারসোর ফোর্থ গ্রেডের সেই চাকরিতে বেতন ৫০,০০০ টাকা থেকে ৭১,২০০ টাকা। ব্যক্তি পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে অন্য কোনো সংস্থার প্রথম শ্রেণিতে ১২ বছর অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর এখানে আবেদন করবেন, চাকরীতে জয়েন করবেন অর্ধেক জীবন চলে যাওয়ার পর, যদি চাকরিটা পান!
স্পারসোর অন্যতম একজন বিজ্ঞানী ড. মোঃ মাহমুদুর রহমান। তিনি ২০০৪ সালে জার্মানির ড্রেসডেন ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি থেকে ডক্টর অফ ন্যাচারাল সায়েন্সেস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০০৭–২০০৯ সালে জাপানের চিবা ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল রিমোট সেন্সিং (CERES) এ পোস্ট–ডক্টরাল গবেষণা পরিচালনা করেন। তার গবেষণার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ফরেস্ট অ্যান্ড ল্যান্ড কভার চেঞ্জ অ্যাসেসমেন্ট, বনের বায়োমাস এবং কার্বন স্টক অনুমান, ম্যানগ্রোভ বনের ইকোসিস্টেমের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। তার ৩৯ টি পাবলিকেশন আছে এবং তার সাইটেশন সংখ্যা ৫৩৪২। ২০২৪–২৫ অর্থবছরে তার ‘Mapping Tree Covers in Bangladesh’ এবং ‘Mapping Tidal Mudflats in the Coastal Region of Bangladesh’ শীর্ষক দুইটি গবেষণা প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

স্পারসোর গবেষণা প্রকল্প তালিকার বাইরে ড. মোঃ মাহমুদুর রহমান ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তার বৈজ্ঞানিক কাজের কোনো তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া যায়নি। রিসার্চগেটে স্পারসোর কয়েকজন কর্মকর্তার কিছু পাবলিকেশন পাওয়া যায়। তবে, অধিকাংশই কৃষি, মৎস্য বা বন্যার পূর্বাভাস সম্পর্কিত গবেষণা। অতীতে এখানকার বিজ্ঞানীদের অর্জন বলতে শুধু স্পারসোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ড. এ এম চৌধুরীর ১৯৯৮ সালে স্বাধীনতা পদক পাওয়ার ব্যাপারে জানা যায়।
- অবকাঠামোগত দুর্বলতাকে আমরা স্পারসোর ব্যর্থতার তৃতীয় কারণ হিসেবে বিবেচনা করছি।
স্পারসোর ওয়েবসাইটের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম ১৬ টি কারিগরি বিভাগ, ৫ টি সহায়ক শাখা এবং সাভারে অবস্থিত একটি আঞ্চলিক দূর অনুধাবন কেন্দ্রের (RRSC) সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। বিভাগগুলো নিম্নরুপঃ
- কৃষি বিভাগ
- পানি সম্পদ বিভাগ
- বন বিভাগ
- ভূতত্ত্ব বিভাগ
- মৎস্য বিভাগ
- সমুুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ
- যান্ত্রিক এবং উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ বিভাগ
- গ্রাউন্ড স্টেশন বিভাগ
- আলোকচিত্র বিভাগ
- মানচিত্রাংকন বিভাগ
- বায়ুমন্ডল গবেষণা বিভাগ
- অ্যাগ্রো অ্যান্ড হাইড্রোমেটিওরোলজি বিভাগ
- মহাকাশ পদার্থবিজ্ঞান ও রকেট গতিবিদ্যা
তাদের ওয়েবসাইট অনুযায়ী ১৩টি বিভাগ লিস্টেড। কিন্তু আরেকটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় ‘যান্ত্রিক এবং উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ বিভাগ’, ‘এগ্রো এন্ড হাইড্রোমেটিওরোলজি বিভাগ’ এবং ‘মহাকাশ পদার্থবিজ্ঞান ও রকেট গতিবিদ্যা’ – এই তিনটি বিভাগকে আলাদা আলাদা ৬টি বিভাগ হিসেবে বিবেচনা করলে মোট ১৬টি বিভাগ হয়। অর্থাৎ, এই বিভাগগুলো সম্মিলিতভাবে ১৩টি বিভাগ হয়ে কাজ করছে। সহায়ক শাখাগুলো হচ্ছে প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখা, হিসাব ও বাজেট শাখা, তথ্য শাখা, ভাণ্ডার ও সংগ্রহ শাখা এবং নিরাপত্তা শাখা।
জনবল সংকটের কারণে বেশিরভাগ কারিগরি বিভাগ নামমাত্রই চালু আছে। কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে একাধিক বিভাগের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এমনকি বন বিভাগের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরই রকেট প্রযুক্তি বিভাগ দেখার মত ঘটনাও ঘটেছে এখানে। এ ছাড়া স্পারসোর মহাকাশ উৎক্ষেপণ স্টেশন, নিজস্ব অরবিট, স্যাটেলাইট এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি সম্পর্কিত গবেষণাগারও নেই। স্পারসোর আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষায়িত কোনো টেলিস্কোপ আদৌ আছে কিনা, সে বিষয়েও কোনো তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া যায় নি। তবে, Design and Assemble of Optical Telescope for Space Observation and Astronomical Research Capacity Building in SPARRSO শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্পের Phase–1 এর জন্য ২০২৩–২৪ অর্থবছরে ১৩ লাখ ২০ হাজার টাকা এবং Phase–2 এর জন্য ২০২৪–২৫ অর্থবছরে ১৯ লাখ ৮০ হাজার টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়। ১২ই জুন, ২০২৪ তারিখে তাদের ফেসবুক পেজে 16″/400 mm Dobsonian telescope দিয়ে তোলা চাঁদের কিছু ছবি পোস্ট করা হয়, পেজটিতে আকাশের ছবি নিয়ে প্রথম পোস্ট ছিল এটাই! উল্লেখ্য, পোস্টটির ক্যাপশন AI দিয়ে লেখা। এছাড়া পেজটিতে শুধুই বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্যাপন, বিভিন্ন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং গুটি কয়েক গবেষণা প্রকল্পের ছবি পোস্ট করা হয়।

এশিয়া প্যাসিফিক স্পেস কো–অপারেশন অর্গানাইজেশনের সদস্যদেশ হওয়ায় সংগঠনটির কাছ থেকে অনুদান হিসেবে বাংলাদেশ একটি সাধারণ মানের জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন পেয়েছে, যা পরীক্ষামূলক পর্যায়ে চালু হয়েছে। এটিই বর্তমানে দেশের একমাত্র গ্রাউন্ড স্টেশন, যার মাধ্যমে স্যাটেলাইট থেকে ডাটা গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা হয়। কখনো অন্য দেশের স্যাটেলাইটের ডেটা কিনে, কখনো বিনা পয়সায় বিদেশি স্যাটেলাইট থেকে ডেটা নিয়ে গবেষণা করেন স্পারসোর বিজ্ঞানীরা।
 সাভারে পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে ৮ একর জমিতে ১৯৮৫ সালে ফ্রান্স সরকারের ঋণে স্পারসোর আঞ্চলিক দূর অনুধাবন কেন্দ্র স্থাপিত (আরআরএসসি) হয়। কিন্তু সেটা পুরোদমে কার্যক্রমে যাওয়ার আগেই ফ্রান্স সরকার সহায়তা বন্ধ করে দেয়। কয়েক বছর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলার পর বন্ধ হয়ে যায় আরআরএসসি। স্পারসোর আইনের ৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকবে এবং এটা প্রয়োজনবোধে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশের যেকোনো স্থানে শাখা কার্যালয়, গবেষণা কার্যালয় ও গবেষণাগার স্থাপন করতে পারবে। অথচ ১৯৮৫ সালে সাভারে আরআরএসসি স্থাপন ছাড়া স্পারসো সম্প্রসারণের আর কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এদিকে ISRO ভারত জুড়ে একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে কাজ করে। ব্যাঙ্গালোরে ইউআররাও স্যাটেলাইট সেন্টারে স্যাটেলাইট ডিজাইন এবং তৈরি করা হয়, আহমেদাবাদের স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে তৈরি হয় পে–লোড এবং সেন্সরগুলো।
সাভারে পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে ৮ একর জমিতে ১৯৮৫ সালে ফ্রান্স সরকারের ঋণে স্পারসোর আঞ্চলিক দূর অনুধাবন কেন্দ্র স্থাপিত (আরআরএসসি) হয়। কিন্তু সেটা পুরোদমে কার্যক্রমে যাওয়ার আগেই ফ্রান্স সরকার সহায়তা বন্ধ করে দেয়। কয়েক বছর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলার পর বন্ধ হয়ে যায় আরআরএসসি। স্পারসোর আইনের ৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকবে এবং এটা প্রয়োজনবোধে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশের যেকোনো স্থানে শাখা কার্যালয়, গবেষণা কার্যালয় ও গবেষণাগার স্থাপন করতে পারবে। অথচ ১৯৮৫ সালে সাভারে আরআরএসসি স্থাপন ছাড়া স্পারসো সম্প্রসারণের আর কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এদিকে ISRO ভারত জুড়ে একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে কাজ করে। ব্যাঙ্গালোরে ইউআররাও স্যাটেলাইট সেন্টারে স্যাটেলাইট ডিজাইন এবং তৈরি করা হয়, আহমেদাবাদের স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে তৈরি হয় পে–লোড এবং সেন্সরগুলো।
- শিক্ষাব্যবস্থা ও সামাজিক বাস্তবতা মহাকাশ গবেষণায় বাংলাদেশের দুর্দশার চতুর্থ কারণ।
বাংলাদেশের মহাকাশ গবেষণায় পিছিয়ে থাকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিভিন্ন কারণ রয়েছে। প্রত্যক্ষের চেয়ে পরোক্ষ কারণই এই খাতে দেশকে এতটা পিছিয়ে দিয়েছে।
প্রত্যক্ষ কারণটি হচ্ছে বাংলাদেশে মহাকাশবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার কোনো সুযোগ নেই বললেই চলে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই মহাকাশবিজ্ঞান বিষয়ক কোন সাবজেক্ট আলাদাভাবে পড়ানো হয় না। ২০০৭ সালে এমআইএসটি প্রথম অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং নামক একটি বিভাগ চালু করে। ২০১৯ সালে দেশে এভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সংসদে বিল পাস হলে ঐ বছরই লালমনিরহাটে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়’ (বর্তমানে বাংলাদেশ এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি) প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা দেশের একমাত্র এভিয়েশন সংক্রান্ত বিশেষায়িত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

এখানে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে অ্যারোস্পেস, অ্যাভিওনিক্স, এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি পড়ানো হয়। কিন্তু, ২০২০ সালে কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর পিকো–স্যাটেলাইট বিষয়ক একটি গবেষণা ছাড়া মহাকাশ গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়টির অন্য কোনো সাফল্যের তথ্য বিভিন্ন সংবাদপত্র ঘেঁটেও পাওয়া যায়নি।
পরোক্ষ কারণ মূলত দুইটি। প্রথমত, আমাদের স্কুল–কলেজের সিলেবাসে ক্রিটিক্যাল থিংকিং, প্রবলেম সলভিংসহ কোনো ধরনের জটিল বিষয় নিয়ে ভাবার লেশমাত্র সু্যোগ নেই। ব্রিটিশদের কেরানি উৎপাদনের ফরমুলা মেনে তৈরি মুখস্থ নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্র–ছাত্রীদের সিলেবাসের বাইরে ভাবতেই শেখায় না। ২০২৩–২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ জিডিপির মাত্র ১.৭৬ শতাংশ ছিল, যা গত ১৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সুতরাং, এদেশে মহাকাশবিদ্যায় ভালো পড়াশোনার সুযোগ চাওয়া একপ্রকার বিলাসিতাই! উপরন্তু, দেশে ‘পাশের বাসার আন্টি’র মতো ব্যঙ্গাত্মক কিন্তু ভয়াবহ এক প্রভাবক রয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের উপর অতিরিক্ত মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। খেয়াল করে দেখবেন, জেন–জি’র একাংশ প্রায়ই বলে তারা ছোটবেলায় মহাকাশবিজ্ঞানী হতে চাইতো। সমাজের অনধিকার চর্চা এবং গোল্ডেন পেয়ে যোগ্যতা প্রমাণের দৌড়ে জিততে গিয়ে তাদের এই স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে গেছে। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, এই শিক্ষাব্যবস্থা এবং সমাজ একটা গোটা জেনারেশনকে ইনফ্যান্টাইল লিভারে গতাসু করে ছেড়েছে। ফলে, স্কুলজীবনে জোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের ছেলে–মেয়েদের আগ্রহ থাকলেও তারা সেটা কাজে লাগাতে পারে না। বিজ্ঞানীর অভাবে স্পারসোকে যে কতটা ভুগতে হচ্ছে, তা আমরা দ্বিতীয় ভাগে ব্যাখ্যা করেছি।

দ্বিতীয়ত, দেশের অনেক মানুষ এখনও দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। দিনকে দিন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে মানুষের পেট চালানোই দায় হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানী ও গবেষকদের না আছে কোনো আর্থিক নিরাপত্তা, আর না আছে প্রয়োজনীয় সাহায্যের কোনো ব্যবস্থা। অনেক ক্ষেত্রে নিজ উদ্যোগেই গবেষণা করেন তারা। উপরন্তু আছে লাগামহীন দুর্নীতি এবং অনিয়ম। এতকিছুর মাঝেও ইন্টারনেটের সুবাদে উঠতি বয়সি তরুণ–তরুণীদের মাঝে মহাকাশ বিষয়ক গবেষণার প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। তারা স্বেচ্ছায় মহাকাশ গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। দেশীয় গুটিকয়েক অলিম্পিয়াডও আছে। প্রতিবছরই আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে যোগদান করে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে জায়গা করে নেয়। যারাও বা এসব প্রতিযোগিতা কিংবা গবেষণামূলক কাজের সঙ্গে সংযুক্ত, তাদের প্রায় সকলেই নিজ উদ্যোগে কিংবা ফান্ড যোগাড় করে নিজেদের কার্যক্রম চালিয়ে থাকে, সরকার থেকে তেমন কোনো সাহায্য পাওয়া যায় না। তাও দেশের বর্তমান প্রজন্ম আজকাল গবেষণাধর্মী কাজের প্রতি বেশ আগ্রহী হচ্ছে যা একপ্রকার শুভলক্ষণই বলা যায়, কিন্তু উন্নত দেশগুলোর জন্য। কারণ এরা কেউই স্পারসোতে যোগ দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে আগ্রহী না। আগ্রহ না থাকাটাই স্বাভাবিক, অস্বাভাবিকভাবে আগ্রহ থাকলেও তারা কখনো সুযোগ পাবে না অসম্ভব রকমের আবেদন যোগ্যতার জন্য।
- স্পারসোর ব্যর্থতার পঞ্চম কারণ সঠিক জায়গায় কোলাবোরেট না করা এবং অপ্রয়োজনীয় প্রকল্পে অর্থ ব্যয়।
নাসা গত বছর জুনে কমার্শিয়াল স্পেস সেক্টরে উন্নয়নের জন্য সাতটি বেসরকারি সংস্থার সাথে কোলাবোরেট করে। Artemis মিশনেও তারা স্টারশিপ নিয়ে স্পেস–এক্সের সাথে কাজ করছে। ভারতের ISRO ২০২১ সালে রকেট তৈরির জন্য Skyroot এবং Agnikul নামের দুটি স্টার্টআপের সাথে চুক্তি সাইন করেছে। এতে করে Agnikul তাদের single piece 3D–printed semi–cryo engine টেস্ট করে সফলতা পেয়েছে এবং Skyroot তাদের launch vehicle development programme নিয়ে কাজ করেছে। প্রায় সব দেশই স্পেস ইন্ডাস্ট্রিতে উন্নতির জন্য প্রাইভেটাইজেশনকে গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশের বেসরকারী দুইটি মহাকাশ গবেষণা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে Amateur Experimental Rocketry Dhaka এবং ধুমকেতু–এক্স।
AERD এর সাথে বাংলাদেশের কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানেরই কোলাবোরেশন নেই। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবং ড. আনোয়ারুল আবেদীন ইনস্টিটিউট অব ইনোভেশন এর সাথে কোলাবোরেশনে এখন পর্যন্ত তাদের দুইটি সাফল্য আছে। ২০২৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারা দেশের প্রথম হাইব্রিড রকেট ইঞ্জিন Pyraflux–01 টেস্ট করেছে। ২০২৪ সালের ১২ই জানুয়ারি AIUB ক্যাম্পাস থেকে তাদের প্রথম weather balloon, Akashbani V1 লঞ্চ করা হয়। দুইটি প্রজেক্টেই তারা সফলতা পেয়েছে। AERD তাদের যাত্রা শুরু করে ২০২৩ এর আগস্টে।

এদিকে ধূমকেতু এক্স দেশের প্রথম সাউন্ডিং রকেট ‘পুঁটিমাছ’ লঞ্চ করার জন্য বিখ্যাত। ২০২২ সালের নভেম্বরে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের এটুআই প্রজেক্টের রকেট্রি চ্যালেঞ্জে ১২৪ টিমের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে ‘ধূমকেতু এক্স’ ৫০ লাখ টাকার অনুদান পায়। ২০২৩ এর ২৫শে নভেম্বর এটুআই, কেবিনেট ডিভিশন, আইসিটি ডিভিশন, ইউএসআইডি এবং বাংলাদেশ এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটির সাথে কোলাবোরেশনে তৈরী ‘ধুমকেতু এক্স–২১’ রকেটটি জনসমক্ষে প্রদর্শনও করে সংস্থাটি; যা ২০২৪ এর ফেব্রুয়ারিতে অফিসিয়ালি লঞ্চ করার কথা ছিল। ধুমকেতু এক্সের ফাউন্ডার নাহিয়ানের একটি ফেসবুক পোস্ট থেকে জানা যায় রকেট লঞ্চের অনুমতি ঝুলছে প্রায় দুই বছর ধরে। আবার, DhumketuX রকেট ল্যাব স্থাপন করার জন্য আইসিটি মন্ত্রণালয় অর্থায়ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, সেটারও কোন অগ্রগতি হয়নি। ধূমকেতু–এক্সের সাথে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কোলাবোরেশন মূলত ফান্ড ভিত্তিক; তবে সেখানেও অনিয়ম দেখা যাচ্ছে, যা দুর্নীতির লক্ষণ। তাদের ওয়েবসাইটে স্পারসোর সাথে কোলাবোরেশনের কথা উল্লেখ থাকলেও ধূমকেতু এক্সের কোনো কার্যক্রমেই স্পারসোকে দেখা যায় নি।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে JAXA, JICA, AIT, CSSTEAP, APSCO, ICIMOD, ESCAP এবং ACRSB এর সাথে কোলাবোরেশনের উল্লেখ স্পারসোর ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়, তবে কোনো বিস্তারিত তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া যায় নি। দেশীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কোলাবোরেশনের কথা লেখা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে কোলাবোরেশনের অবস্থা যে কেমন, তা ভার্সিটি পড়ুয়া শিক্ষার্থীরাই ভালো বলতে পারবেন।
বিদেশি কোলাবোরেশনগুলোতে বিভিন্ন জটিলতা থাকতে পারে; বা দাবি করা কোলাবোরেশনগুলো আদৌ আছে কি না, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত না। তাছাড়া স্পেস ইন্ডাস্ট্রিতে উন্নতি করতে হলে দেশীয় কোলাবোরেশনে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। AERD বা ধুমকেতু–এক্সের সাথে স্পারসোর কোলাবোরেশন তাদের প্রযুক্তিগত উন্নতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। সমস্যা হচ্ছে, স্পারসোর বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনিয়ার রিক্রুটিং এর জঘন্য প্রসেসের জন্য এখানে উচ্চতর গ্রেডগুলোতে তরুণদের অংশগ্রহণ নেই। উপরন্তু এখানকার প্রায় সব গবেষণা প্রকল্পই কৃষি, বন, নদী বা সমুদ্র ভিত্তিক। এক কথায় মহাকাশ প্রযুক্তির সাহায্যে মহাকাশ বাদে অন্য সকল সেক্টরে কাজ করে স্পারসো। যেই প্রজেক্টগুলো দেশীয় কোলাবোরেশনে থাকা অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর করার কথা। এ ধরণের প্রজেক্ট একই সাথে স্পারসোর জন্য ক্ষতিকর এবং দেশের জন্য অলাভজনক। AERD দুই বছরের কম সময়ে এবং ধুমকেতু–এক্স গত আট বছরে যা অর্জন করেছে, তা স্পারসো ৪৫ বছরেও অর্জন করতে পারেনি। ২০০৮–০৯ থেকে ২০২০–২১ পর্যন্ত ১১ অর্থবছরে মাত্র ১১৭ টি গবেষণা করা হয়েছে, অর্থাৎ বছরে গড়ে ১১ টি গবেষণা– ১৬টির (বা ১৩টির) মধ্যে কিছু কিছু বিভাগ বছরে একটা গবেষণাকর্মও প্রকাশ করে নি।
২০২৪–২৫ অর্থবছরে স্পারসোর ২৫টি গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে Mapping Tree Covers in Bangladesh অথবা, Development of a Humanoid Robot অথবা, Study and Investigate on Solar Chromosphere with Hydrogen–Alpha (656 nm) Narrow Bandpass (Phase–1) ইত্যাদির মত বেশিরভাগ প্রজেক্টই রিভিউ রিসার্চ, রিমোট সেন্সিং আর স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ সম্পর্কিত। যে প্রজেক্টগুলো স্পারসো হাতে নিচ্ছে সেগুলো সম্পন্ন করার মতো সক্ষমতা হয়তো বা আছে। কিন্তু এসব দেশের জন্য অতটা প্রয়োজনীয় বা যথেষ্ট অ্যাডভান্সড প্রজেক্ট না।
একটা প্রকৃত স্পেস অর্গানাইজেশনের যেমন প্রজেক্ট নেওয়া দরকার, স্পারসো তেমন প্রজেক্ট নিচ্ছে না, আবার সেরকম প্রজেক্ট নেওয়ার মতো ইনফ্রাস্ট্রাকচারও নেই। ফলে, এসব গবেষণা দেশের জন্য ইতিবাচক তেমন কোনো ভুমিকা রাখে না। অথচ উল্লিখিত ৫টি প্রকল্পের জন্য খরচ হচ্ছে ৮৩ লাখ ১৩ হাজার ১৭৫ টাকা। ইউএসের NOAA আর জাপানের GMS থেকে ডাটা নিয়ে ভূমি জরিপ করা অথবা ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস দেওয়ার কাজ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মত প্রতিষ্ঠানগুলোর, কোনো জাতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার না। Inventory of Water Bodies for Fisheries Resources Using High Resolution Satellite Sensor Data অথবা Bank–line Shifting and Sandbar Dynamics of the Teesta River Using Multi–Temporal Satellite Images এর মত প্রকল্প প্রকারান্তে অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই না। বরং এই প্রকল্পগুলো স্পারসোর সক্ষমতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক, এসবের পরিবর্তে ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন নিয়ে কাজ করলে বেশি লাভজনক হতো। তবে Agro–Climatic Environmental Monitoring Project এর জন্য স্পারসো ১৯৮৬ সালে নাসার ‘Group Achievement Award’ লাভ করে।
- স্পারসোর ব্যর্থতার ষষ্ঠ কারণ দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক প্রভাব।

ভারতের ইসরো শুধু মহাকাশ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সীমাবদ্ধ নয়, তারা আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে যোগাযোগ, কৃষি, আবহাওয়া এবং শিক্ষাখাতে স্যাটেলাইট ব্যবহার করে সরকারকে বোঝাতে পেরেছে জাতীয় উন্নয়নে ইসরো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। কিন্তু তার আগে ইসরো প্রযুক্তিগতভাবে নিজেদের শক্তিশালী করেছে, আর্থিক সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও তারা রকেট উড়িয়ে দেখিয়েছে। এমনকি, non–magnetic environment প্রয়োজন হওয়ায় গরুর গাড়িতে স্যাটেলাইট পরিবহনের মতো কাজও করেছে তারা। ভারতের প্রথম স্যাটেলাইট আর্যভট্টের পুরোটাই ছিল ইসরোর ডিজাইন করা। তারা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ছাড়া কৃষি বা অন্যান্য খাতে ভূমিকা রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে নি। বাংলাদেশ সরকার এই প্রযুক্তিগত উন্নয়নেই ভূমিকা রাখে নি। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট লঞ্চের বিভিন্ন ঘটনা থেকে বোঝা যায় হাসিনা সরকার স্পারসোকে একরকম ইচ্ছাকৃতভাবেই পিছিয়ে রেখেছিল।

প্রায় ৩০০০ কোটি টাকার বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট–১ বাংলাদেশকে কোনো লাভ তো দিতে পারেই নি, বরং উৎক্ষেপণের পর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৭ বছরে প্রায় ৭৫০ কোটি টাকা লস করেছে। সম্পূর্ণ প্রজেক্টটাই ছিল লোক দেখানো ‘উন্নয়ন’, এজন্য বিটিআরসির বার্ষিক ফাইন্যান্স রিপোর্টে গড়মিল পর্যন্ত করা হয়। স্পারসোকে উপেক্ষা করে, দেশের প্রথম স্যাটেলাইট নিয়ে কাজ করার ন্যূনতম সুযোগ পর্যন্ত না দিয়ে প্রজেক্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণটাই আউটসোর্স করা হয়। স্যাটেলাইট মেইনট্যানেন্সের জন্য নতুন করে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাছাড়া স্পারসো যে ধরণের গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়, সেগুলোতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট–১ এর মতো কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোনো ভূমিকাই রাখতে পারে না। প্রজেক্ট অনুমোদনের সময় বলা হয়েছিলো, স্যাটেলাইটটি ফ্লাড মনিটরিং, ওয়েদার ফোরকাস্টিং এবং নদী ও উপকূলীয় সীমার ম্যাপিং করার মত কাজও করতে পারবে। এদিকে থ্যালিস আলেনিয়া স্যাটেলাইটটি ডিজাইনই করেছে টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিসের জন্য। অবশ্য ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট লঞ্চিং প্রজেক্ট’ দেশব্যাপী ইনোভেটিভ আইসিটি সলিউশন প্রদান করার জন্য ২০১৬ সালে আইটিইউ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে স্পারসো গত ৫ বছরে গবেষণা প্রকল্পগুলোতে মোট ১০ কোটি টাকাও বরাদ্দ পায় নি, সেখানে স্যাটেলাইটের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয় ২৯৬৮ কোটি টাকা।
এত সব দুর্নীতির মধ্যে প্রথম স্যাটেলাইট থেকে এক পয়সা লাভ পাওয়ার আগেই ২০১৯ এর ১৪ নভেম্বর বিএসসিএল চেয়ারম্যান শাহজাহান মাহমুদ জানিয়েছিলেন, তিন থেকে চার মাসের মধ্যে দ্বিতীয় স্যাটেলাইট নির্ধারণে পরামর্শক নিয়োগের কথা। কোভিডের কারণে পিছিয়ে ২০২১ এর ২০ জানুয়ারি ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট–২’–এর ধরন নির্ধারণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফ্রান্সের প্রাইস–ওয়াটারহাউস–কুপার্সকে ১ কোটি ৫৬ লাখ টাকার চুক্তিতে নিয়োগ দিয়েছিল বিএসসিএল, যা স্পারসোর গত ৫ বছরে মোট গবেষণা প্রকল্পে পাওয়া অর্থায়নের ২০ শতাংশ। সেদিনই সরকার ২০২৩ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট–২ উৎক্ষেপণ করার ঘোষণা দেয়। ২০২২ সালে চিপ আমদানিতে রাশিয়ার ওপর আমেরিকান নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও রসকসমস– এর অঙ্গসংস্থা গ্লাভকসমস এর সাথে সমঝোতা–স্মারকও স্বাক্ষর করেছিল বিএসসিএল। হাস্যকরভাবে সরকার বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ৩ ও ৪ নিয়েও চিন্তা–ভাবনা শুরু করেছিল। স্যাটেলাইট লঞ্চ করা এক রকমের শখই হয়ে উঠেছিল সরকারের। তবে, এই অ্যাবসোলিউট সিনেমার কোনো চরিত্রেই জায়গা হয় নি স্পারসোর। এমনকি কোন ধরনের স্যাটেলাইট পাঠানো উচিত হবে, সেই সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা বা যোগ্যতা– কোনোটাই ছিল না স্পারসোর। অথচ, চাইলেই এই প্রজেক্টগুলোর মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া যেত বাংলাদেশের মহাকাশ গবেষণাকে।
মহাকাশ গবেষণায় দুর্নীতির আরেক নজির ছিল ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্পেস অবজারভেটরি’। মুজিব জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে এই প্রকল্পের অবজারভেটরি টাওয়ারটির উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১০০ মিটার! দেশের কোটি কোটি শিক্ষার্থীর আবেগের সাথে এক রকম প্রহসনই করেছিলেন প্রজন্মের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক ও বিজ্ঞানী মুহম্মদ জাফর ইকবাল। এই প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে এখানে পড়তে পারেন।
এছাড়া যে কোনো পোস্টে নিয়োগের ক্ষেত্রে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি এবং রাজনৈতিক প্রভাবের প্রশ্ন তো বাংলাদেশের যে কোনো সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তোলা যায়। উল্লেখ্য, ভারতের ইসরো রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত। জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের পরিবর্তন হলে ইসরোর চেয়ারম্যান পরিবর্তন হয় না। গবেষক এবং ইঞ্জিনিয়ার ব্যতীত ইসরো কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগ দেয় না। ইসরোর চেয়ারম্যানও এর আওতাভুক্ত। সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে ইসরো নির্দিষ্ট ইনস্টিটিউটকে প্রাধান্য না দিয়ে স্কিল এবং অভিজ্ঞতাকে উপরে রাখে।
২০২০ সালে উন্নয়নের লক্ষ্যে স্পারসো কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। সরকারের রূপকল্প অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করার কথা। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে দুটি স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপন এবং দেশের উপযোগী আর্থ–অবজারভেটরি স্যাটেলাইট ডেভেলপমেন্ট ও অরবিটে স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই করা। ২০২৪ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করার কথা থাকলেও এটি এখনো ঝুলন্ত অবস্থাতেই রয়েছে। কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়া হলেও কোনো কূলকিনারা হয় নি। মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে আর্থ–অবজারভেশন উন্নয়নের লক্ষ্যে ল্যাব স্থাপন, টেলিস্কোপ স্থাপন, নিজস্ব রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট অরবিটে স্থাপন ইত্যাদি রয়েছে। যদিও ভবিষ্যতে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোনো সম্ভাবনা নেই। হাজারো অনিয়মের মধ্যে শুধু একটি দালান হিসেবেই দাঁড়িয়ে আছে স্পারসো।
-
ভূ–রাজনীতিও বাংলাদেশের মহাকাশ গবেষণায় পিছিয়ে থাকার একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে।
বিংশ শতকের কোল্ড ওয়ারে জেতার লক্ষ্যে রুশ এবং মার্কিন বিজ্ঞানীরা মহাকাশ গবেষণায় বিপ্লব নিয়ে আসেন। সামরিক ইন্টার–কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল থেকে শুরু হয় আধুনিক রকেটের যাত্রা। সে যুদ্ধের জের ধরেই প্রথম স্যাটেলাইট পাঠানো, চাঁদে মানুষ পাঠানো থেকে শুরু করে সৌরজগতের বাইরে পর্যন্ত মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে। একবিংশ শতকে মহাকাশ প্রতিযোগিতা আবারও ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে; যেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন, জাপান, ভারত এবং রাশিয়া। মহাকাশ ক্রমেই জাতীয় শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্র হয়ে উঠছে।
অনেক দেশ অতীতে মহাকাশ গবেষণায় বিভিন্ন রকমের বাধার সম্মুখীন হয়েছে। ভারতের ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন, যাতে করে তারা চন্দ্রবিজয় করেছে, সেটার ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয়েছিল জটিলতা। ১৯৯১ সালে ভারত এবং রাশিয়ার মধ্যে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন সরবরাহের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির অধীনে রাশিয়া ভারতকে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন সরবরাহের পাশাপাশি এর টেকনোলজি হস্তান্তর করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলি এই চুক্তির বিরোধিতা করে। যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা ছিল এই প্রযুক্তি সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতে পারে, বিশেষ করে ব্যালিস্টিক মিসাইল তৈরিতে। তারা রাশিয়ার উপর চাপ প্রয়োগ করে চুক্তি বাতিল করার জন্য। যুক্তরাষ্ট্র Missile Technology Control Regime এর অধীনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার হুমকি দেয়। ফলস্বরূপ, রাশিয়া টেকনোলজি হস্তান্তরের অংশ থেকে সরে আসে। তবে, তারা চুক্তির অংশ হিসেবে ভারতকে দুটি ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন দিয়েছিল। এসময় ইসরোর জন্য নিজস্ব প্রযুক্তিতে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন ডেভেলপ করা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এই বাধা সত্ত্বেও, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে স্বনির্ভরভাবে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন তৈরি করতে সক্ষম হন এবং চন্দ্রযান– ২, চন্দ্রযান– ৩ এর মতো প্রজেক্ট সফল হয়।
এমনকি বাংলাদেশ স্যাটেলাইট লঞ্চ করার সময়ও ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিটের কাছে আপত্তি জানিয়েছিল ভারত। জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবীর বিষুবরেখা অঞ্চলে প্রায় ৩৬ হাজার কিলোমিটার উপরে একই অল্টিটিউডে অবস্থান করে। বঙ্গবন্ধু–১ স্যাটেলাইটটি বাংলাদেশের নিকটবর্তী বিষুবরেখা অঞ্চলে থাকার কথা। কিন্তু এটি অবস্থান করছে ইন্দোনেশিয়ার উপর ১১৯.১ ডিগ্রিতে বাংলাদেশের সাথে ৪৫ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। এর কারণ হলো ২০১৭ সাল থেকে বাংলাদেশের বিষুবীয় অঞ্চলে ভারতের GSAT–17 স্যাটেলাইট অবস্থান করছে। আগে বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলো APSTAR–7 স্যাটেলাইট ব্যবহার করত, যা বাংলাদেশের উপরে ৯০ ডিগ্রিতে অবস্থান করছে; এর মাধ্যমে একদিকে দুবাই এবং অন্যদিকে মালয়েশিয়া পর্যন্ত সম্প্রচারের সুবিধা পাওয়া যেত। কিন্তু, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের অবস্থানের কারণে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত সরাসরি পৌঁছনো সম্ভব না, আরেকটি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছাতে হবে।

বঙ্গবন্ধু–১ স্যাটেলাইটের জন্য ২০১৪ সালে দুইটি অরবিটাল স্লট আবেদন করলেও একটি স্লটে অন্যান্য ২০টি দেশের আবেদন এবং আরেকটিতে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও চায়নার বিরোধিতার কারণে ITU দুটি স্লটই রিজেক্ট করে দেয়। বর্তমান অরবিটাল স্লটটি রাশিয়ার Intersputnik International Organization of Space Communication এর কাছ থেকে ২১৮ কোটি টাকায় ৪৫ বছরের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সালের মে মাসেই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ২ এর জন্য নিজস্ব ১০০ ডিগ্রি ইস্ট এবং ৭৪ ডিগ্রি ইস্ট অরবিটাল স্লট আবেদন করে সরকার। ১০০ ডিগ্রি ইস্টের জন্য ভারতও আবেদন করেছে।
এসব থেকে বোঝা যায় বিশ্ব–রাজনীতিতে স্যাটেলাইট এবং রকেট লঞ্চ করার সক্ষমতা কতটা গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশের রকেট লঞ্চ করার সক্ষমতা দক্ষিণ এশিয়াসহ বিশ্ব রাজনীতিকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করবে, যা স্পারসোকে পিছিয়ে রাখার অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কারণ হিসেবে অনুমান করা যায়। একটি স্পেস লঞ্চপ্যাড স্থাপন করতে চাইলে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের বিকল্প নেই। তাও প্রশ্ন থেকে যায়, বাংলাদেশে রকেট লঞ্চপ্যাড স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা কি আসলেই আছে?
একটি লঞ্চপ্যাড নিয়মিত রকেট উৎক্ষেপনে সক্ষম হলে তা দেশের অর্থনীতিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। নতুন কর্মসংস্থান তৈরি, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, দুর্যোগ মোকাবেলায় সহযোগিতা, রক্ষণখাতে সুবিধাসহ আরও অসংখ্য ক্ষেত্রে দেশের জন্য সুফল বয়ে আনতে পারে। তবে হাতেগোনা কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া বিজ্ঞানের অন্যান্য খাতে বাংলাদেশের যে বেহাল অবস্থা, সেখানে স্পেস প্রোগ্রামের পরিসর বাড়াতে স্পেস লঞ্চপ্যাড স্থাপন বিলাসিতা। তাছাড়া নিজস্ব লঞ্চপ্যাড বা মহাকাশযান ছাড়াও যে উন্নত স্পেস প্রোগ্রাম ও গবেষণা চালানো সম্ভব, তার প্রমাণও প্রচুর।
বাংলাদেশে স্পেস লঞ্চপ্যাড স্থাপন ব্যয়বহুল হওয়ার পেছনে ভৌগোলিক কারণও রয়েছে। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি দেশগুলো রকেট লঞ্চ করার জন্য আদর্শ। কারণ এখানে পৃথিবীর ঘূর্ণন বেগ সবচেয়ে বেশি, যা রকেট লঞ্চে অতিরিক্ত সুবিধা দেয়। যদিও বাংলাদেশ ঠিক নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অবস্থিত নয়, তবে দেশের দক্ষিণাঞ্চল এক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা দিতে পারে। তাছাড়া লঞ্চিং সাইট সাধারণত বড় জলাশয়ের কাছাকাছি স্থাপন করতে হয়, যাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় এবং উৎক্ষেপণকালে রকেটের ধ্বংসাবশেষ জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পড়ার ঝুঁকি কমে। এই দিক থেকেও বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূল উপযুক্ত মনে হতে পারে। তবে এখানেও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসব জায়গা সারাবছরই ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকির মধ্যে থাকে, যা রকেট লঞ্চের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজ অত্যন্ত জটিল করে দেয়। তাছাড়া বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকিতেও রয়েছে, তাই রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র বানাতে চাইলে অবকাঠামোর দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। এখানে জাপানের উদাহরণ দেওয়া যায়। দেশটির প্রায় চার ভাগের তিন ভাগই পাহাড়, নিরক্ষরেখা থেকেও অনেক দূরে। দ্বীপ রাষ্ট্র, প্রায় প্রতিদিন ভূমিকম্প, সুনামি – এসব লেগে থাকা সত্ত্বেও তারা তানেগাশিমা স্পেস সেন্টার থেকে নিজস্ব রকেট লঞ্চ করে।

এক কথায়, ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ রকেট লঞ্চের জন্য একেবারে আদর্শ নয়, তবে পুরোপুরি অনুপযোগীও নয়। আদৌ লঞ্চপ্যাড স্থাপন করা হবে কি না, তা নির্ভর করে মহাকাশ গবেষণায় বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর। আর এটি অনেকাংশেই নেতিবাচক।
-
পরিস্থিতি উন্নয়নে স্পারসোর ফিউচার প্ল্যান যেমন হওয়া উচিতঃ
মহাকাশ গবেষণার সুফল যে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোও নানাভাবে পেতে পারে, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ভারত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট মনিটরিং এর মাধ্যমে বন্যার গতিপথ, ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস সহ সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পরিবর্তন আনা সম্ভব। এটি কৃষি, নগর পরিকল্পনা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাতেও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। মহাকাশ গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে টেলিকমিউনিকেশন, রোবোটিক্স এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটবে। বিনিয়োগ বাড়ালে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিদেশি প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা কমিয়ে এনে নিজস্ব স্যাটেলাইট ব্যবস্থার মাধ্যমে সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সীমান্ত নজরদারি এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হবে।
বাংলাদেশের গবেষণা খাতে ব্যয় করা হয় মোট জিডিপির মাত্র ০.৩০ শতাংশ। ২০২৪ সালের তথ্যমতে, দেশে গবেষণা খাতে মাথাপিছু ব্যয় হয় মাত্র ৬২০ টাকা। দেশের প্রতি ১০ লাখ মানুষের বিপরীতে গবেষক আছেন মাত্র ১০৭ জন। মোট গবেষকের মধ্যে নারী গবেষক মাত্র ১০.৮২ শতাংশ। গবেষণায় বাংলাদেশের খরচ হয় সবচেয়ে বেশি কৃষি খাতে, সে তালিকার চতুর্থ অবস্থানেও নেই মহাকাশ খাত। মৌলিক গবেষণা কাজেও কোনো ব্যয় করা হয় না। এ অবস্থায় স্পারসোকে এগিয়ে নিতে হলে একে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। স্পারসোর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে যোগ্যতা সম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে। এক্ষেত্রে শুধু ডিগ্রি বিবেচনায় আনলেই হবে না; ব্যক্তির গবেষণার ইতিহাস, প্রকাশিত রিসার্চ পেপারের মান, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে অভিজ্ঞতার মত দিকও লক্ষ্য রাখতে হবে।
দেশে যে এভিয়েশন ইউনিভার্সিটি তৈরি করা হয়েছে, সেখানে উন্নত মানের তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ও প্রয়োগমূলক গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার মান এতটা উন্নত করতে হবে যেন, সেখান থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীকে পরবর্তীতে স্পারসোতে গবেষক হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেয়া যায়। স্পারসোর সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা–কর্মচারীদের উপযুক্ত বেতন–ভাতা ও সুযোগ–সুবিধা প্রদান করতে হবে, যেন গবেষণা কার্যে মনোনিবেশ করতে গিয়ে তাদের পেটের চিন্তা না করতে হয়। মহাকাশ গবেষণায় নারী গবেষকের সংখ্যা প্রায় অপ্রতুল বললেই চলে। নারী গবেষকদের জন্য গবেষণার নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিসহ সুস্থ ও বৈষম্যবিহীন পরিবেশে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
বাংলাদেশের গবেষণাগারগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয়। উপযুক্ত গবেষণাগার সৃষ্টির জন্য যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ নিতে হবে। নিজস্ব স্যাটেলাইট স্টেশন ও টেলিস্কোপ স্থাপনের মত বিষয়ে নজর দিতে হবে। স্পারসোকে মহাকাশ বিষয়ক কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানে রূপদান করতে হবে। দেশব্যাপী বিভিন্ন জেলায় মহাকাশ গবেষণা বিষয়ক উপ–প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যেগুলো স্পারসোর সাথে সমন্বয় করে কাজ করবে। নভোথিয়েটারে কয়েকটা গ্রহ–উপগ্রহ ঝুলিয়ে রাখা ছাড়াও মহাকাশ বিষয়ক সেমিনার আয়োজন, থ্রিডি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে মহাকাশ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়কে ভিউজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করতে হবে।
স্কুলজীবন থেকে শিক্ষার্থীদের মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে স্পারসোর সহযোগিতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। স্পারসোর গবেষকদের তত্ত্বাবধানে স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের গবেষণায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। পাশাপাশি, বাংলাদেশে মহাকাশ গবেষণার পরিবেশ গড়ে তুলতে অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকদের এদেশে কাজ করার সুযোগ প্রদান করতে হবে।
তবে, যেকোনো প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করতে গেলেই প্রয়োজন হয় বিশাল অংকের বিনিয়োগ এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি। দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিশাপ কাটিয়ে উঠে একদিন স্পারসো ঘুরে দাঁড়াবে, এই আমাদের প্রত্যাশা।
প্রতিবেদকঃ
প্লাবন গোস্বামী (কন্টেন্ট রিসার্চ এক্সিকিউটিভ, সায়েন্স বী)
সহযোগিতায়ঃ
জোবায়দা রহমান মাঈশা, আতিয়া শেহরীন, দিবা বিশ্বাস, রাফিয়া রুহী, সুবহা মাহমুদ নীতি, মুহাম্মদ মোহ্তাসিম, মুহাইমেনুল ইসলাম নাফিস
(কন্টেন্ট রিসার্চ টিম, সায়েন্স বী)
তথ্যসূত্রঃ- প্রথম আলো, টেক টাইমস, স্কাই.ওআরজি, স্পার্সো.গভ